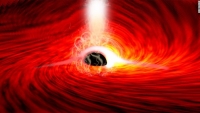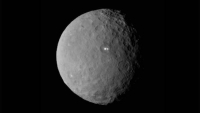শুক্রবার ● ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১
প্রথম পাতা » সূর্যগ্রহণ » সৌরকলঙ্ক (Sunspot)
সৌরকলঙ্ক (Sunspot)
 পর্যবেক্ষণ করলে সূর্যের উজ্জ্বল আলোর মাঝে ছোট কালো দাগ পরিলক্ষিত হয়, যা আমাদের কাছে সৌরকলঙ্ক নামে পরিচিত। প্রাচীন কালের গ্রীক ইতিহাস থেকে জানা যায়, আজ থেকে শত শত বছ পূর্বে যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি, তখন মানুষ খালি চোখে কোন কোন সময়ে জ্বলন্ত সূর্যের বুকে ছোট-বড় গাঢ় কালো রঙের দাগ প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের মধ্যে একদলের ধারণা ছিল যে ঐ গভীর কালো দাগগুলো আসলে সূর্যপৃষ্ঠের কোন কিছু নয়, ওগুলো গ্রহ, সূর্যের পৃষ্টদেশের ওপরে অবস্থানের কারণে ওগুলোকে কালো দাগের মত দেখায়। আবার কারো কারো মতে ওগুলো সূর্যের পর্বত। কিন্তু বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি সেই পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে প্রমাণ করলেন ওগুলো কোন গ্রহ হতে পারে না। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি প্রত্যক্ষ করেন কালো দাগগুলো সূর্যপৃষ্ঠের ওপর আড়াআড়িভাবে স্থান পরিবর্তন করে। শুধু তাই নয়, এরা সবসময় একই দিকে থাকে এবং একই গতিতে স্থান পরিবর্তন করে। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের সাপেক্ষে এই দাগগুলোকে কালো মনে হলেও এগুলো মোটেই কালো নয়। শুধুমাত্র ঘিরে থাকা আলোকমন্ডলের তুলনায় এদের রেডিয়েশন বিতরণ অপেক্ষাকৃতভাবে কম বলে সূর্যের অন্যান্য জায়গার চেয়ে এসব জায়গার তাপ অনেকটা কম, তাই চারপাশের অতি উজ্জ্বলতার মাঝে এদের নিসপ্রভতায় অনেকটা কালচে বলে মনে হয়।
পর্যবেক্ষণ করলে সূর্যের উজ্জ্বল আলোর মাঝে ছোট কালো দাগ পরিলক্ষিত হয়, যা আমাদের কাছে সৌরকলঙ্ক নামে পরিচিত। প্রাচীন কালের গ্রীক ইতিহাস থেকে জানা যায়, আজ থেকে শত শত বছ পূর্বে যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি, তখন মানুষ খালি চোখে কোন কোন সময়ে জ্বলন্ত সূর্যের বুকে ছোট-বড় গাঢ় কালো রঙের দাগ প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের মধ্যে একদলের ধারণা ছিল যে ঐ গভীর কালো দাগগুলো আসলে সূর্যপৃষ্ঠের কোন কিছু নয়, ওগুলো গ্রহ, সূর্যের পৃষ্টদেশের ওপরে অবস্থানের কারণে ওগুলোকে কালো দাগের মত দেখায়। আবার কারো কারো মতে ওগুলো সূর্যের পর্বত। কিন্তু বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি সেই পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে প্রমাণ করলেন ওগুলো কোন গ্রহ হতে পারে না। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি প্রত্যক্ষ করেন কালো দাগগুলো সূর্যপৃষ্ঠের ওপর আড়াআড়িভাবে স্থান পরিবর্তন করে। শুধু তাই নয়, এরা সবসময় একই দিকে থাকে এবং একই গতিতে স্থান পরিবর্তন করে। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের সাপেক্ষে এই দাগগুলোকে কালো মনে হলেও এগুলো মোটেই কালো নয়। শুধুমাত্র ঘিরে থাকা আলোকমন্ডলের তুলনায় এদের রেডিয়েশন বিতরণ অপেক্ষাকৃতভাবে কম বলে সূর্যের অন্যান্য জায়গার চেয়ে এসব জায়গার তাপ অনেকটা কম, তাই চারপাশের অতি উজ্জ্বলতার মাঝে এদের নিসপ্রভতায় অনেকটা কালচে বলে মনে হয়।
সৌরকরঙ্কের দুইটি অংশ আছে, কেন্দ্রীয় অংশটি খুব অন্ধকার বলে এটি প্রচ্ছায়া (Umbra)। অপর অংশটি একে ঘিরে থাকে, যা অপেক্ষাকৃত কম অন্ধকার, এটি উপচ্ছায়া (Penumbra)। গবেষণায় দেখা গেছে, সৌরকলঙ্কগুলো ছোট বড় যাই হোক না কেন কখনো এরা সমান সংখ্যায় থাকে না। ১৭০০ থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা যায়, সৌরকলঙ্কগুলো সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় আর বৃদ্ধি পায় না। ঠিক ঐ অবস্থাটিকে বলা হয় ‘সানস্পট মেক্সিমা’। ঐ অবস্থা থেকে ওরা আবার আস্তে আস্তে সংখ্যায় কমতে শুরু করে এবং এমন একটা সংখ্যায় আসে যা থেকে আর কমে না। এ অবস্থাটাকে বলা হয় ‘সানস্পট মিনিমাম’। গড়পড়তা ১১ বছর পর পর ‘সানস্পট মেক্সিমা’ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এই ১১ বছর সময়কালটিকে বলা হয় ‘সৌরকলঙ্ক চক্র’ বা Sunspot cycle।








 ২১ জুন বাংলাদেশ থেকে দৃশ্যমান আংশিক সূর্যগ্রহণ
২১ জুন বাংলাদেশ থেকে দৃশ্যমান আংশিক সূর্যগ্রহণ  ২৬ জানুয়ারি, ২০০৯
২৬ জানুয়ারি, ২০০৯